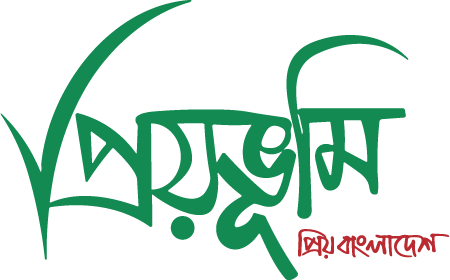

আপিল বিভাগের রায় ও বিতর্কের সূত্রপাত
গত মঙ্গলবার বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ একটি ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করে, যেখানে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICT) কর্তৃক জামায়াতে ইসলামীর নেতা এটিএম আজহারুল ইসলামকে প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডের রায় বাতিল করা হয়। এই রায়ের মাধ্যমে আজহারুল ইসলাম কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং মুক্ত হওয়ার পরপরই তিনি রাজধানীর শাহবাগে উপস্থিত হয়ে দলের সমর্থকদের সংবর্ধনা গ্রহণ করেন।
এই রায় শুধুমাত্র একটি আইনি সিদ্ধান্তই নয়, বরং এটি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। আজহারুল ইসলামের মুক্তিকে একদল “বিচারিক স্বাধীনতার জয়” হিসেবে দেখলেও, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের ভুক্তভোগী পরিবারগুলো এই সিদ্ধান্তকে "ইতিহাসের মুখে চপেটাঘাত" বলে অভিহিত করছে।
মামলার পটভূমি: কী ছিল অভিযোগ?
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আজহারুল ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ ছিল অত্যন্ত গুরুতর:
গণহত্যা: ১৯৭১ সালে রংপুর অঞ্চলে ১,২৫৬ জন বেসামরিক নাগরিককে হত্যার ঘটনায় তার ভূমিকা প্রমাণিত হয়েছিল।
ধর্ষণ ও নির্যাতন: কমপক্ষে ১৭ জনকে অপহরণ এবং একজন নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ ছিল তার বিরুদ্ধে।
লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ: শতাধিক বাড়িঘরে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তার সম্পৃক্ততা ট্রাইব্যুনালে প্রমাণিত হয়েছিল।
২০১৪ সালে ট্রাইব্যুনাল তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও, আপিল বিভাগ এই রায় বাতিল করে বলেছে, “আরোপিত অভিযোগ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি।”
আপিল বিভাগের রায়ে উল্লেখযোগ্য দিক
প্রমাণের অভাব: আপিল বিভাগের মতে, ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ আজহারুলের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমাণে অপর্যাপ্ত ছিল।
আইনি প্রক্রিয়ার ত্রুটি: রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, ট্রাইব্যুনালে সাক্ষীদের জেরা ও প্রমাণ সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় “প্রক্রিয়াগত দুর্বলতা” ছিল।
রাষ্ট্রপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা: মামলার শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা আজহারুলের পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেননি, যা রায়কে প্রভাবিত করেছে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।
প্রতিক্রিয়া: উল্লাস নাকি ক্ষোভ?
জামায়াত-শিবিরের উল্লাস: আজহারুলের মুক্তিকে “আইনের শাসনের জয়” বলে অভিহিত করে জামায়াত ও ইসলামী ছাত্রশিবির। শাহবাগে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আজহারুল জুলাই আন্দোলনকারীদের ধন্যবাদ জানান, যারা ২০১৩ সালে আইন সংশোধনের মাধ্যমে আপিলের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।
ভুক্তভোগীদের বেদনা: রংপুরের এক ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য বলেন, “আমার বাবাকে হত্যার বিচার আজ ধূলিসাৎ হলো।”
সরকার ও সুশীল সমাজ: সরকার এই রায়কে “বিচার বিভাগের স্বাধীনতা” বলে মেনে নিলেও, মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রশ্ন তুলেছে: “প্রমাণের অভাব থাকলে, নতুন করে তদন্ত কেন হয়নি?”
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন: ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার কীভাবে?
প্রমাণ সংকট: যদি ট্রাইব্যুনালে প্রমাণ অপর্যাপ্ত ছিল, তাহলে নতুন করে তদন্ত ও মামলা দায়েরের উদ্যোগ নেওয়া যায় কি না?
রাষ্ট্রের ভূমিকা: রাষ্ট্রপক্ষ কেন আজহারুলের পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেনি? এটি কি আইনগত অবহেলা, নাকি রাজনৈতিক সমঝোতা?
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট: অন্যান্য দেশে যুদ্ধাপরাধের মামলায় আপিলে রায় পরিবর্তন হলে নতুন করে তদন্ত হয় (যেমন: রুয়ান্ডা ট্রাইব্যুনাল)। বাংলাদেশে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় কি না?
ইতিহাসের দায়: আমরা কি ভুলে যাব?
১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল, তা ইতিহাসের অমোঘ সত্য। আজহারুলের রায় এই প্রশ্ন তুলে দেয়: “বিচারের নামে কি আমরা সেই ইতিহাসকে অস্বীকার করতে পারি?”
ভুক্তভোগীদের অধিকার: যাদের পরিবারের সদস্যরা নিহত হয়েছেন, তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে।
ট্রাইব্যুনালের ভবিষ্যৎ: এই রায়ের পর অন্যান্য যুদ্ধাপরাধী মামলার আপিল কীভাবে পরিচালিত হবে, তা নিয়ে আইনবিদদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।
ন্যায়বিচার নাকি আইনের ফাঁক?
আজহারুল ইসলামের রায় একটি আইনি সিদ্ধান্ত হলেও, এটি সমাজে গভীর বিভেদ তৈরি করেছে। একদিকে বিচারিক প্রক্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করা জরুরি, অন্যদিকে ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ বিবেচনা করা যেতে পারে:
পুনরায় তদন্ত: নতুন প্রমাণ সংগ্রহ করে মামলাটি পুনর্বিবেচনার আবেদন করা।
আইনি সংস্কার: যুদ্ধাপরাধ মামলায় আপিল প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা।
ভুক্তভোগীদের সহায়তা: ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য মানসিক ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা।
সর্বোপরি, এই রায় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বিচার শুধু আইনের বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়—এটি ইতিহাস, ন্যায় ও মানবিকতার সমন্বয়ে গঠিত হতে হবে।
তথ্যসূত্র:
দৈনিক প্রথম আলো, প্রোবাংলা, ডেইলি স্টার (জুলাই-আগস্ট ২০২৪ সংখ্যা)
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায় ও আপিল বিভাগের দলিল
ভুক্তভোগী পরিবার ও আইনজীবীদের সাক্ষাৎকার
মন্তব্য করুন